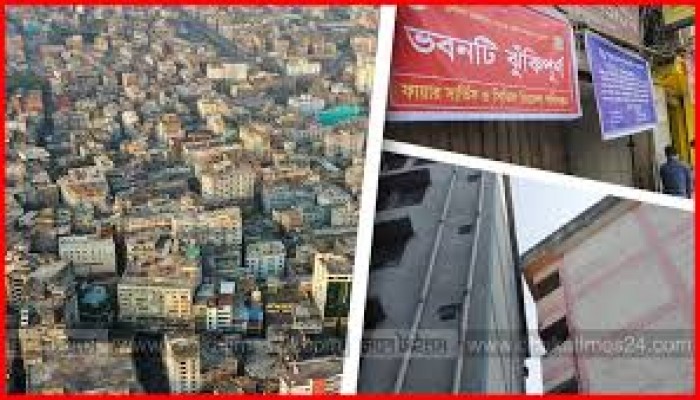* ’দোদুল্যমান’ রাজনীতিতে নতুন নতুন মেরুকরণ
* পিআর পদ্ধতির ভোট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া
* পিআর পদ্ধতি চায় ১৮ দল আপত্তি ২৮ দলের
* পিআর পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদ্ধতিগত দিক নিয়ে একমত হতে পারছেন না না রাজনৈতিক দলগুলো। পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে এ নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না সরকার। পিআর পদ্ধতিতে ভোট চায় চায় ১৮ দল আপত্তি ২৮ দলের। তবে কোনো পক্ষ নেবে না অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তাদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করুক তারা কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে চায়। ফলে ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত ‘নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন’ তাদের দীর্ঘ প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত সুপারিশ করা থেকে বিরত থেকেছে। এমতাবস্থায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন গতানুগতিক কিংবা তত্তাবধায়ক পদ্ধতিতে হবে, না-কি সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে হবে তা নির্ভর করছে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ওপর। তবে সবমিলিয়ে ’দোদুল্যমান’ রাজনীতিতে নতুন নতুন মেরুকরণের ছক আঁকছে দলগুলো। ফলে আসন্ন নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কমিশন, যদিও পিআর পদ্ধতি চায় ১৮ দল আর বিরোধীতা করে আপত্তি জানিয়েছে ২৮ টি রাজনীতিক দল। তবে পিআর পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না বলে জানা গেছে।
পিআর পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই: নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চালুর বিষয়ে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট সতর্কতা জানিয়েছে। কমিশনের মতে, এ পদ্ধতি কার্যকর হলে দেশের নির্বাচনব্যবস্থা দলনির্ভর হয়ে পড়বে এবং সাধারণ মানুষ সরাসরি কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার অধিকার হারাবে। সেই সঙ্গে বড় রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব আরও বেড়ে যাবে, ক্ষুদ্র দলগুলোর কাছে বড় দলগুলো জিম্মি হয়ে পড়তে পারে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ ও ড. মো. আবদুল আলীম জানিয়েছেন, পিআর পদ্ধতিতে ভোটাররা আর কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন না, বরং দিতে হবে দলকে। এর ফলে সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগই থাকবে না। গত ৫০ বছরের সংসদীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নিয়েছেন এবং অনেকে জয়ী হয়ে সংসদে গেছেন। তবে পিআর পদ্ধতি চালু হলে এ প্রক্রিয়া বিলুপ্ত হবে বলে কমিশনের পর্যবেক্ষণ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান সময় ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পিআর পদ্ধতি চালুর পক্ষে রাজনৈতিক ঐকমত্য নেই। ফলে কমিশন এ বিষয়ে কোনো সুপারিশ করেনি। বরং পদ্ধতিটির ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলো তুলে ধরেছে। পিআর পদ্ধতিতে এককভাবে কোনো দলের পক্ষে সরকার গঠন করা কঠিন হবে। বড় দলগুলো ক্ষুদ্র দলের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হবে। এতে সরকার গঠন ও টিকে থাকায় লেনদেন, চাপ ও আপসের প্রবণতা বাড়বে।
জানা গেছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি এখন আলোচনার কেন্দ্রে। দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি পিআর পদ্ধতির কঠোর বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ কিছু রাজনৈতিক দল এই পদ্ধতির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এ নিয়ে দলগুলোর পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্য রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। তারপরও দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কিছু মৌলিক বিষয়ে সংস্কারে চলছে জোর চেষ্টা। এর অংশ হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়া কী হবে সেটা আলোচিত হচ্ছে। তবে
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তার প্রতিবেদনে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা এবং পিআর পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও আগামী নির্বাচন কোন্ পদ্ধতিতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করেনি। সুপারিশের জায়গায় বলা হয়, রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবের কারণে নির্বাচন পদ্ধতি পরির্তনের বিষয়ে কোনোরূপ সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি সম্পর্কে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্মানিত রাজনীতিবিদদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৫টি। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে চারটি দলের নিবন্ধন বাতিল রয়েছে এবং আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে। ফলে, ৫০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৮টি দল পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের পক্ষে। বিপক্ষে অবস্থান ২৮টি দলের। চারটি দল তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। কিছু দল আংশিকভাবে এই পদ্ধতির পক্ষে। বিপক্ষে থাকা দলগুলো মূলত বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের সঙ্গী। এর বাইরে জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) পিআর পদ্ধতির পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। মূলধারার ইসলামী দলের মধ্যে পাঁচটি দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে, দুটি বিপক্ষে এবং দুটি দল অবস্থান পরিষ্কার করেনি। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতামূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুই ধরনের দায়বদ্ধতা বিরাজমান। একটি নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা, আরেকটি সমান্তরাল দায়বদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে যদি ভোটের জন্য জনগণের দোরগোড়ায় ধরনা দিতে হয়, তাহলেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে এবং তাদের জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করতে হয়। কারণ, অপকর্ম ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লে জনগণের পক্ষে সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হবে। এভাবেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমান্তরাল দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় কমিটি ও অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের সল্ডিয় হওয়া সম্ভব হয় এবং তারা নির্বাহী বিভাগকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। সরকারের পক্ষে তখন আর অন্যায় এবং অপকর্ম করে পার পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। একইভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নগ্ন দলীয়করণের শিকার হয় না এবং তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে সকল সরকারি কার্যল্ডমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশে বর্তমানে আসনভিত্তিক ‘ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট’ (এফপিটিপি) বা আসনভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি একটি জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি। আমাদের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে “একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য” নিয়ে জাতীয় সংসদ। তবে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পর আরপিও অনুযায়ী নিবন্ধন স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে নতুন মেরুকরণ। বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও নিবন্ধন স্থগিত হওয়ায় এ মুহূর্তে দেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) পাশাপাশি আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৃথিবীর ১৭০টি দেশের মধ্যে অর্ধেকের মতো দেশে নির্বাচন হয় সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। যেটিকে বলা হয় প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর। এই পদ্ধতিতে একটি দল যত ভোট পায়, সেই অনুপাতে জাতীয় সংসদে আসন লাভ করে। এতে একটি নির্বাচনের পর সংসদে সব দলের ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকে। এর কিছু ইতিবাচক দিক যেমন আছে তেমনি নেতিবাচক দিকও আছে। উন্নত দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেটি আমাদের দেশে হলে তো ভালোই হবে। কিন্তু ভালো করতে গিয়ে খারাপ হলে আবার সমস্যা। তাই টেকসই চিন্তা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নতুন এই পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যখন ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। সেখানে দুই ধরনের মতই পাওয়া গেছে। কেউ কেউ নতুন পদ্ধতি হিসেবে পিআরকে স্বাগত জানালেও বেশির ভাগই আগামী নির্বাচন এই পদ্ধতিতে হোক সেটা চান না। তারা বলছেন, এই পদ্ধতির ভালো কিছু দিক থাকলেও এখনই বাংলাদেশের জন্য তা উপযোগী হবে না। এই পদ্ধতি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে। এছাড়া এসব বিষয়কে ইস্যু বানালে নির্বাচন ঝুলে যেতে পারে বলেও কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন। তবে নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি নিয়ে খেটে খাওয়া সাধারন মানুষ কিছুই জানেন না বলে জানান। কী পদ্ধতিতে ভোট হবে সেটার চেয়ে তাদের কাছে ভোট যেন নিরপেক্ষ ও অবাধ হয় সেটাই তারা চান। অনেক বছর ধরে ভোট দিতে পারেন না জানিয়ে দ্রুত সময়ে যেন ভোটের আয়োজন করা হয় সেই দাবি তোলেন তারা। ঢাকায় রিকশা চালান রংপুরের রইস মিয়া। তিনি বলেন, ভোট-টোট বুঝি না, আমাদের পেটে কেউ লাথি না দিলেই হবে। আমরা খেটে-খেয়ে বাঁচতে চাই। মিরপুর এলাকার স্টেশনারি দোকানি আব্দুস সালাম বলেন, দেশের যে পরিস্থিতি তাতে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া জরুরি। কারণ দীর্ঘদিন মানুষ ভোট দিতে পারেনি। তাই আমাদের দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতেই নির্বাচন হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী তামিম হোসেন বলেন, দেশের সব কিছু যেহেতু সংস্কার হচ্ছে, তাই আগামীতে যাতে কেউ আর শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচার হতে না পারেন সেটির জন্য সব কিছু সংস্কার করতে হবে। তাই নির্বাচনসহ সবকিছু আরও উন্নত হওয়া চাই। একই কথা বলেছেন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জলিল হোসেন। তিনি বলেন, দেশের যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সেটি পরিপূর্ণভাবে করা উচিত। নির্বাচনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবকিছুর সংস্কার হওয়া উচিত। তারপর দেশের নাগরিকদের জন্য যেটা ভালো হয় সেটা করা উচিত। উন্নত দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেটি আমাদের দেশে হলে তো ভালোই হবে। কিন্তু ভালো করতে গিয়ে খারাপ হলে আবার সমস্যা। তাই টেকসই চিন্তা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বেসরকারি একটি স্কুলের শিক্ষক আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, আসলে নির্বাচনের আমেজ যে কী জিনিস দেশের মানুষ সেটা ভুলেই গেছে। তাই নির্বাচনের আমেজ ফিরিয়ে আনতে যা যা করার সব করা উচিত। নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো নিরপেক্ষতা। সেটি ঠিক থাকলেই চলবে। আর নতুন কিছু নয়, বরং প্রচলিত নিয়েমেরই নির্বাচন চাই। মিরপুর-১২ এলাকার সাবেক ওয়ার্ড কউন্সিলর প্রার্থী মালেক হোসেন বলেন, হুট করে নতুন কোনো পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সেটি অনেকের অজানা থাকবে। দেশের মানুষকে কোনো বিষয়ে সঠিকভাবে জানানোর আগে তেমন নির্বাচন করা ঠিক হবে না। কারণ নতুন এই পদ্ধতির ব্যাপারে অনেকেই জানেন না। তাই প্রচলিত নিয়মেই একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই বরং ভালো হবে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কেমন হবে: ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকার সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করে। এ জন্য সংবিধান সংশোধনে ৫৮(ক) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়। ২০১০ সালে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পরবর্তী দুইবার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা থাকতে পারবে। তবে বিচারপতিদের দূরে রাখতে হবে এ ব্যবস্থা থেকে। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাই বিলোপ করে দেয়। গত বছরের ডিসেম্বরে হাইকোর্ট এই সংশোধনী বাতিল করে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফেরাতে ত্রয়োদশ সংশোধনী পুনর্বহালে আপিল বিভাগে রিভিউ করেছে বিএনপি ও জামায়াত। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আশা করছেন আদালতের রায়ে ফিরবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা। ২০০৬ সালে সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে বিএনপিপন্থি আখ্যা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিরোধিতায় আন্দোলন করেছিল আওয়ামী লীগ। এতে কে এম হাসান সরে দাঁড়ালে, পরবর্তী সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন।
জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, তাদের দল চায় সাবেক প্রধান বিচারপতিদের একজন হবেন প্রধান উপদেষ্টা। যদি সাবেক প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা পদে গ্রহণযোগ্য কাউকে নিয়োগ করবেন। তবে ২০০৬ সালের অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে চান না তারা। ডা. তাহের বলেন, জামায়াতের দাবি, স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে হতে হবে। এ প্রস্তাব নাকচ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক পাঁচ বছর হতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক থেকে দূরে রাখার বিষয়ে তিনি বলেছেন, জুডিশিয়ারিকে বাদ রেখে আরও দু-একটি পথ যদি রাখা যায়, যাতে সবার গ্রহণযোগ্যতায় প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ হয়, আলোচনা হতে পারে। তবে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব বলেছেন, যখনই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হয়, তখনই দেশে সংঘাত হয়। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে এনসিপি নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা দিয়েছে। রূপরেখা তুলে ধরে জাবেদ রাসিন বলেন, তত্ত্বাবধায়কে প্রধান বিচারপতিকে রেখে বিচারালয়ের রাজনীতিকরণ করা হয়েছিল। তাই নিম্নকক্ষের সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বাছাইয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। তা ব্যর্থ হলে ভোটের অনুপাতে (পিআর) গঠিত উচ্চকক্ষ প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে।
নিউজটি আপডেট করেছেন : Dainik Janata
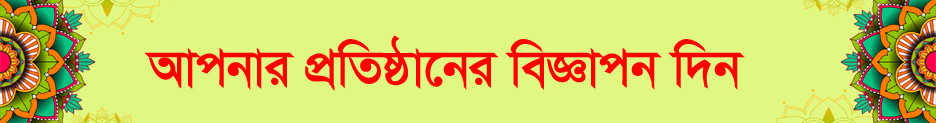
সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কমিশন
ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে
- আপলোড সময় : ০৬-০৭-২০২৫ ০৩:২৭:০১ অপরাহ্ন
- আপডেট সময় : ০৬-০৭-২০২৫ ০৩:২৭:০১ অপরাহ্ন

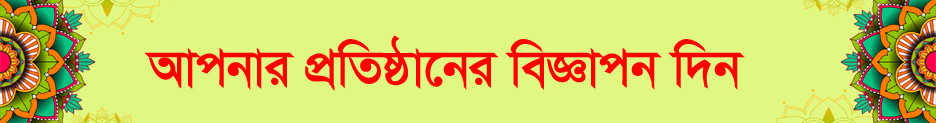
কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ

 সফিকুল ইসলাম
সফিকুল ইসলাম